
চলনবিল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য—অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদের গবেষণার আলোকে
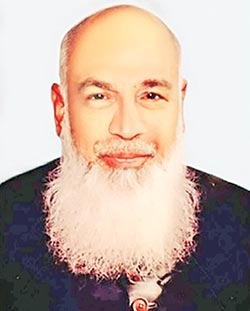 বাংলাদেশের হৃদয়ে বিস্তৃত এক অনন্য ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল হলো চলনবিল। নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থাকা এ জলাভূমি কেবল একটি ভৌগোলিক স্থানই নয়, এটি গ্রামীণ সংস্কৃতি, কৃষি, মৎস্য, লোকসাহিত্য ও ইতিহাসের এক অমূল্য ভাণ্ডার। এই চলনবিলের অতীত, বর্তমান ও ঐতিহ্যকে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদ।
বাংলাদেশের হৃদয়ে বিস্তৃত এক অনন্য ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল হলো চলনবিল। নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে থাকা এ জলাভূমি কেবল একটি ভৌগোলিক স্থানই নয়, এটি গ্রামীণ সংস্কৃতি, কৃষি, মৎস্য, লোকসাহিত্য ও ইতিহাসের এক অমূল্য ভাণ্ডার। এই চলনবিলের অতীত, বর্তমান ও ঐতিহ্যকে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদ।
তাঁর লেখা চলনবিলের ইতিকথা ও চলনবিলের লোকসাহিত্য আজও গবেষক, পাঠক ও সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে। তাঁর গবেষণা শুধু বই নয়, বরং চলনবিলের মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্থান পেয়েছে।
চলনবিল বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল–ভূপ্রকৃতি, লোকজ সংস্কৃতি ও জলজ জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য ভূখণ্ড। এই অঞ্চলকে নিয়ে যে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রতিষ্ঠানগত উদ্যোগ আজও গবেষকদের নিত্য-উৎস, তার শীর্ষে আছেন চলনবিলেরই সন্তান অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদ। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ‘চলনবিলের ইতিকথা’ ও ১৯৮১ সালে প্রকাশিত ‘চলনবিলের লোকসাহিত্য’—এই দুই গ্রন্থে তিনি চলনবিলের ইতিহাস, প্রকৃতি ও লোকঐতিহ্যের তথ্যসম্বলিত দলিলভাণ্ডার গড়ে দেন। একই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে খুবজীপুরে প্রতিষ্ঠা করেন চলনবিল জাদুঘর, যা ১৯৮৯ সালের ২ জুলাই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে আসে—চলনবিল-গবেষণার জন্য এটি আজও একটি মুখ্য নিবাস।
চলনবিলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য
অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদ চলনবিলকে শুধু একটি জলাশয় হিসেবে নয়, বরং প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের বিস্ময়কর ভূখণ্ড হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন— বর্ষাকালে চলনবিল এক বিশাল সাগরের রূপ নেয়, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১৩ থেকে ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। শুষ্ক মৌসুমে এটি পরিণত হয় উর্বর কৃষিজমিতে। ফলে এখানকার মানুষের জীবনধারা পুরোপুরি আবর্তিত হয় পানি ও জমিকে ঘিরে।
কৃষি ও অর্থনীতি
চলনবিল অঞ্চলের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো কৃষি। ধান, পাট, গম, আখ, ডালসহ নানা ফসল উৎপাদনে এ অঞ্চলকে তিনি বাংলাদেশের খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পাশাপাশি মাছের প্রাচুর্য এ অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে। এম. এ. হামিদ লিখেছেন—
“চলনবিলের মাছ শুধু এখানকার মানুষের জীবিকা নয়, বরং সমগ্র বাংলার খাদ্যাভ্যাসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।”

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি
এম. এ. হামিদের অন্যতম অবদান হলো চলনবিলের লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। তিনি এ অঞ্চলের পালাগান, জারি-সারি, ভাওয়াইয়া, মঙ্গলগান, পুঁথিপাঠ, কীর্তন প্রভৃতি ধারা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর মতে, চলনবিলের মানুষের জীবনযাপন, সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম ও স্বপ্ন এই গান ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।
এছাড়া স্থানীয় মেলা, হাট-বাজার, গ্রামীণ খেলাধুলা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে তিনি চলনবিলের প্রাণস্পন্দন হিসেবে অভিহিত করেছেন।
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
চলনবিল শুধু কৃষি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র নয়, বরং এ অঞ্চলের আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে এটি বাণিজ্য, কৃষি ও নৌযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। তিনি তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, প্রাচীন জনপদের বিকাশে চলনবিলের জলাভূমি ও নদী-নালার ছিল বিশাল ভূমিকা।
এম. এ. হামিদ এ অঞ্চলের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন মসজিদ, মন্দির ও দিঘি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর রচনায় পাওয়া যায়— মুসলিম শাসনামল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত চলনবিল ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।
সামাজিক জীবন
চলনবিলের মানুষের সামাজিক জীবনও এম. এ. হামিদের গবেষণায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তিনি বর্ণনা করেছেন— এখানে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, উৎসবমুখরতা ও অতিথিপরায়ণতা এক অনন্য সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলে। বর্ষায় নৌকাবাইচ, শীতে পিঠা উৎসব, হাট-বাজারের আড্ডা সবই চলনবিলের প্রাণচাঞ্চল্য প্রকাশ করে।

গ্রন্থাবলি ও গবেষণা-দৃষ্টিভঙ্গি
‘চলনবিলের ইতিকথা’ (১৯৬৭): ইতিহাসনির্ভর, বিপুল তথ্যের সমাবেশ—চলনবিলের ভূপ্রকৃতি, নদ-নদীর জাল ও জনপদের গঠন বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে উদ্ধৃত একটি গবেষণাগ্রন্থ।
‘চলনবিলের লোকসাহিত্য’ (১৯৮১): বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত এই বইটি অঞ্চলের লোকধারা নিয়ে সংকলন ও বিশ্লেষণধর্মী কাজ হিসেবে গ্রন্থ-তালিকায় স্বীকৃত।
চলনবিল জাদুঘর (১৯৭৮): ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত; স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিপুল নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণে নিবেদিত। পরে সরকারি তত্ত্বাবধানে আসে।
এই তিনটি অবদান—দুই গ্রন্থ ও একটি জাদুঘর—মিলে চলনবিলের ইতিহাস-ঐতিহ্য নথিবদ্ধ করার এক সমন্বিত কাঠামো দাঁড়ায়, যা আজও নীতি-নির্ধারক ও গবেষকদের রেফারেন্স ফ্রেম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
ভূ-প্রকৃতি ও উৎপত্তি: ইতিকথার আলো
চলনবিল পরপর যুক্ত বহু ‘ডিপ্রেশন’ বা নিম্নভূমির সমষ্টি। বর্ষায় এগুলো মিলেমিশে প্রায় ৩৬৮ বর্গকিমি জলরাশিতে রূপ নেয়; রাজশাহী–পাবনা–সিরাজগঞ্জ (এবং নাটোর) অঞ্চলে এর বিস্তার। ভূতাত্ত্বিকভাবে পদ্মা-যমুনা-তিস্তা-আত্রাই প্রভৃতি নদীর পলিবহন ও গতিপথ-পরিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে এই অববাহিকার সৃষ্টি জড়িত। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে রেল-লাইন ও বাঁধনির্ভর অবকাঠামো এলাকাব্যাপী স্বাভাবিক জলপ্রবাহে বাধা তৈরি করে জলরাশি ও নিষ্কাশন-প্যাটার্নে বড় প্রভাব ফেলে—চলনবিলের জলপরিবেশ বোঝার ক্ষেত্রে এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
নদ-নদী ও জলপথের জাল
ঐতিহাসিক হিসেবে চলনবিল অঞ্চলে প্রায় ৪৭টি নদী ও জলপথ মিলিত হয়েছে—আত্রাই, বড়াল, করতোয়া, ভাদাই, চিকনাই, বরঞ্জা, তেলকুপি ইত্যাদি নিয়ে গড়ে ওঠে বিস্তৃত জল-মহাল, যা বর্ষাকালে একরাশা জলে রূপ নেয় এবং শুষ্ক মৌসুমে খাল-খাঁড়ি-নদীর জটিল নেটওয়ার্কে ভাগ হয়। এই জলপথ-নির্ভরতা স্থানীয় পরিবহন, বাজারীকরণ ও পেশাভিত্তিক বসতির আকৃতি নির্ধারণ করেছে।

বসতি, জীবিকা ও মৌসুমি জীবন
চলনবিলের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে দ্বৈত অর্থনীতিতে অভ্যস্ত—বর্ষায় মৎস্য আহরণ, শুষ্ক মৌসুমে ধানসহ নানাবিধ ফসলচাষ। জলভূমির ওঠানামা যেমন পেশা নির্ধারণ করে, তেমনি খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান-নকশা (উঁচু ভিটা, খড়ছাউনি), যাতায়াত (নৌকা-নির্ভরতা) ও বাজার-সংযোগকেও নির্দেশ করে। জলজ সম্পদের গুরুত্ব ও কর্মসংস্থান বিস্তারের দিকটি আধুনিক গবেষণায়ও পুনঃনিশ্চিত হয়েছে।
লোকঐতিহ্য, কারুশিল্প ও জীবনাচার—‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের পরিসর
‘চলনবিলের লোকসাহিত্য’ গ্রন্থটি অঞ্চলভিত্তিক লোকধারা (কথা-গাথা, গান, আচার-অনুষ্ঠান, লোকশিল্প) নথিবদ্ধ করার জন্য স্বীকৃত সংকলন; চলনবিলের জল-নির্ভর জীবন, পেশা ও ঋতুচক্রের সঙ্গে যুক্ত নানা লোকরীতি—যেমন শিকার/মৎস্যজাল-সংস্কৃতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, পাঁজি-পঞ্জিকার ব্যবহার, গ্রামীণ নৌ-সংস্কৃতি—এই বই ও পরবর্তী গবেষণাগুলোর আলোচ্য। অঞ্চলের আদিবাসী/স্থানীয় জ্ঞানভিত্তিক মাছধরার পদ্ধতি ও সরঞ্জামের বর্ণনা যে চলতি প্রজন্মেও ‘ইন্ডিজেনাস নলেজ’ হিসেবে টিকে আছে, তা সাম্প্রতিক ক্ষেত্রসমীক্ষাতেও উঠে এসেছে।
চলনবিল জাদুঘর: ঐতিহ্যের আর্কাইভ
অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদের প্রতিষ্ঠিত চলনবিল জাদুঘরে সংগৃহীত রয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের নান্দনিক ও নৃ-তাত্ত্বিক দলিল—প্রাচীন পুঁথি, ধাতব মুদ্রা, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, যুদ্ধাস্ত্র, স্থানীয় লোকাচার-সম্পর্কিত পট ও নিদর্শন, মাছধরার সরঞ্জামসহ বহু সামগ্রী; জাদুঘরটি ১৯৮৯ সালে সরকারিভাবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় এলে সংগ্রহের প্রাতিষ্ঠানিক সংরক্ষণ আরও জোরদার হয়। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো জাদুঘরের রক্ষণাবেক্ষণ-চ্যালেঞ্জের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়—যা সমাধানে নীতিনির্ধারণী মনোযোগ প্রয়োজন।
পরিবেশগত চাপ ও সংরক্ষণের প্রয়োজন
চলনবিলের মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে কীটনাশকের বেড়ে যাওয়া ব্যবহার, অবকাঠামোগত বাধা (রেল/সড়কের বাঁধ), অনিয়ন্ত্রিত শিকার—এসবের প্রভাব নিয়ে গবেষণা ও সংবাদভিত্তিক প্রমাণ রয়েছে। একইসঙ্গে জলাভূমি-সেবাগুলো (মৎস্য উৎপাদন, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি-চক্র) আজ ঝুঁকির মুখে—যার প্রতিকার টেকসই জলাভূমি-ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় জ্ঞান-চর্চার ধারাবাহিকতায় সম্ভব। অধ্যক্ষ হামিদের কাজের মধ্যে যে ‘স্থানীয় জ্ঞানের নথিভুক্তি ও জাদুঘর-ভিত্তিক সংরক্ষণ’—তারই আধুনিক সম্প্রসারণ জরুরি।
কেন এম. এ. হামিদ আজও পথপ্রদর্শক
১) স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য নথিভুক্তির প্রাতিষ্ঠানিক মডেল: গ্রন্থ–জাদুঘর–সম্প্রদায়—এই তিন স্তম্ভে তিনি একটি টেকসই কাঠামো গড়েছেন।
২) গবেষণা-উৎসের দুর্লভ সংকলন: ১৯৬৭ ও ১৯৮১ সালের কাজ দুটি আজও ক্ষেত্রসমীক্ষা, নীতিনির্ধারণ ও সাংবাদিকতায় বহুল উদ্ধৃত।
৩) লোকঐতিহ্যকে উন্নয়ন-আলোচনায় আনা: পরিবেশ, জীবিকা ও সংস্কৃতিকে এক ফ্রেমে বিবেচনার ধারায় তিনি আগেভাগেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
চলনবিল নিয়ে তাঁর অবদান
অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদ শুধু ইতিহাস সংরক্ষণেই থেমে থাকেননি, তিনি চলনবিল উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, চলনবিল একদিন আলাদা জেলার মর্যাদা পাবে। এজন্য তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেতু-সড়ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেন। তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য আজো নীতি-নির্ধারক ও গবেষকদের জন্য দিকনির্দেশক।
পরিশেষে বলা যায়,চলনবিলকে বোঝার যে ‘মৌলিক সূত্রপাঠ’—অধ্যক্ষ এম. এ. হামিদের গ্রন্থদ্বয় ও জাদুঘর সেই সূত্রেরই ভিত্তি। জলাভূমির প্রতি রাষ্ট্রীয়-স্থানীয় সুরক্ষা বাড়াতে হলে তার এই নথিভুক্ত ঐতিহ্য ও জ্ঞানভান্ডারকে পাঠ্য, গবেষণা ও নীতি-পর্যায়ে আরও সুসংহতভাবে ব্যবহার করতে হবে। এভাবেই ইতিকথা ও লোকসাহিত্য—দুই ধারার আলোয় চলনবিলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একই সুতায় বাঁধা যায়।
(লেখক ও সাংবাদিক লুৎফর রহমান হীরা)
সম্পাদক ও প্রকাশকঃ লুৎফর রহমান হীরা
হেড অফিসঃ ১/ জি,আদর্শ ছায়ানীড়, রিংরোড, শ্যামলী, আদাবর ঢাকা - ১২০৭।
স্বত্ব © ২০২৫ চলনবিলের সময়